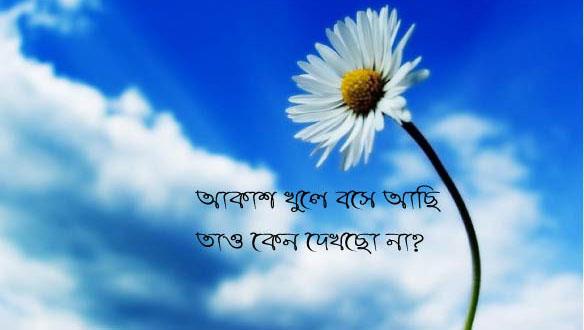বাপ্পা মজুমদার ও সামিনা চৌধারীর ‘এক মুঠো গান’এ্যালবামের “আকাশ খুলে বসে আছি, তাও কেন দেখছো না” গানটা যারা শুনেছেন তারা এর জনপ্রিয়তার কথা জানেন। গানের
এই লাইটি অন্য ভাবেও তো বলা যেত, যেমন “হাঁ করে বসে আছি তাও কেন আসছ না” কিংবা “পসরা সাজায়ে বসে আছি তাও কেন কিনছ না” অথবা “সেজে-গুজে বেড়াতে এসেছি তাও কিছু বলছ না?” কিংবা ধরুন যদি বলি “এত এত
লেখা লিখছি তাও কেন পড়ছ না?” ইত্যাদি, কিন্তু তাতে কি তা এত জনপ্রিয় হত? তাতে কি তা
সাহিত্য হত? হত না কারণ সাহিত্যের ভাষা ভিন্ন, আর তা হল মানুষের মনের ভাষা, জ্ঞানের
ভাষা নয়। সাহিত্য হল মানব মনের প্রতিচ্ছবি, এটি এমন এক আলোর পৃথিবী যেখানে যা আসে
সব আলোকিত হয়ে আসে। এই আকাশ তো নীল আকাশ নয় বরং মনের আকাশ। এই গানের সাথে আমার বেশ
কিছু স্মৃতি জড়িত তাই গানটা হঠাৎ কানে আসলে সেই স্মৃতীগুলো মনে চলে আসে। গানটার গুরুত্বও
আমার কাছে একটু অন্যরকম ও বিশেষ বটে। সেই স্মৃতি নিয়ে কিছু বলার ইচ্ছা নাই এখানে, বরং
পারষ্পরিক ভাব বিনিময় মাধ্যম গুলো নিয়ে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই
যা সচরাচর বলা হয় না বা যে উদ্দেশ্য গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। এই বিষয়ে
রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ “সাহিত্যের সামগ্রী” অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমি প্রবন্ধটি সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করেছিলাম
২০০৪ এ, এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে তা আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। সাধু-তে লেখার চল ইদানীং
উঠে গেছে কিন্তু সাধু ভাষা সেই সময় লেখালেখির ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত ভাষা মনে করা হত।
চলিত ভাষার সুবিধা এই যে, তা বিষয়বস্তুকে স্বচ্ছ ও দ্রুততার সাথে বুঝতে সহায়তা করে।
যুগ-যুগান্তরে মানব মনোভঙ্গি পরিবর্তন হলেও মূল ভাবধারা একই থাকে। আলোচনার সুবিধার
জন্য সাহিত্যের সামগ্রীর উপর লেখা রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান প্রবন্ধটি এখানে সংযোজন
করছি, তার পর আমার বক্তব্য উল্লেখ করব।
<উদ্ধৃতি> একেবারে খাঁটি ভাবে নিজের আনন্দের জন্য লেখা
সাহিত্য নয়। অনেকে কবিত্ব করে বলেন যে, পাখি যেমন নিজের উল্লাসে গান করে লেখকের রচনার
উচ্ছ্বাসও সেরকম আত্মগত, পাঠকেরা যেন তা আড়ি পেতে শুনে থাকেন। পাখির গানের মধ্যে পাখি
সমাজের প্রতি যে কোন লক্ষ্য নাই, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। থাকুক বা না থাকুক তা
নিয়ে তর্ক করা বৃথা। কিন্তু লেখকের রচনার প্রধান লক্ষ্য পাঠক সমাজ। আমাদের মনের ভাবের
একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করতে চায়, প্রকৃতিতে
আমরা দেখি টিকে থাকার জন্য প্রাণীদের মধ্যে সব সময় একটা চেষ্টা চলছে, যে জীব বংশ বিস্তারের
মাধ্যমে যত বেশী জায়গা জুড়তে পারে তার জীবনের অধিকার তত বেশী বেড়ে যায়, নিজের অস্তিত্বকে
সে যেন তত অধিক সত্য করে তোলে। মানুষের মনোভাবের মধ্যে সেরকম একটা চেষ্টা আছে, তফাতের
মধ্যে এই যে প্রাণের অধিকার দেশে কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে। মনোভাবের চেষ্টা
বহু কাল ধরে মনকে আয়ত্ত করা। আমি যা চিন্তা করছি, যা অনুভব করেছি তা মরবে না, তা মন
হতে মনে, কাল হতে কালে, চিন্তিত হয়ে, অনুভূত হয়ে প্রবাহিত হয়ে চলবে। আমরা যে মূর্তি
গড়ছি, ছবি আঁকছি, কবিতা লিখছি, পাথরের মন্দির নির্মাণ করছি, দেশ বিদেশে চিরকাল ধরে
অবিরাম এই যে একটা চেষ্টা চলছে এটা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে
অমরতা প্রার্থনা করছে। সাহিত্যে এই চিরস্থায়িত্বের
চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা। যা জ্ঞানের কথা তা প্রচার হয়ে গেলেই তার উদ্দেশ্য সফল
হয়ে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু হৃদয়ের ভাবের কথা প্রচারের মাধ্যমে পুরাতন হয় না। সূর্য যে
পূর্ব দিকে উঠে, এ কথা আর আমাদের মন আকর্ষণ করে না কিন্তু সূর্যোদয়ের যে সৌন্দর্য ও
আনন্দ তা জীবন সৃষ্টির পর হতে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে অম্লান আছে। রচনা বলতে গেলে,
ভাবের সাথে ভাব প্রকাশের উপায় দুটোকেই সমান ভাবে বুঝায় কিন্তু বিশেষ করে উপায়টাই লেখকের।
দীঘি বলতে জল এবং খনন করা আধার দুই-ই একসঙ্গে বুঝায়। জল মানুষের সৃষ্টি নয় তা চিরন্তন।
সেই জলকে বিশেষ ভাবে সবার জন্য সুদীর্ঘকাল রক্ষা করবার যে উপায় তাই-ই কীর্তিমান মানুষের
নিজের। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ভাবকে নিজের করে সকলের করাই সাহিত্য এবং তাই-ই ললিত কলা।
সাধারণ জিনিসকে বিশেষ ভাবে নিজের করে সেই উপায়েই তাকে পুনরায় বিশেষভাবে সাধারণের করে
তোলাই সাহিত্যের কাজ। যে সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হওয়ার জন্য প্রতিভাশালী
হৃদয়ের কাছে সুর, রং, ইঙ্গিত, প্রার্থনা করে, যা আমাদের হৃদয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি না হয়ে
উঠলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, তাই সাহিত্যের সামগ্রী। তা আকারে-প্রকারে,
ভাবে-ভাষায়, সুরে-ছন্দে মিলে তবেই বাচতে পারে। তা মানুষের একান্ত আপনার – তা আবিষ্কার
নয়, অনুকরণ নয়, তা সৃষ্টি। <অন-উদ্ধৃত>
সাহিত্যের সামগ্রীতে কবিগুরু সাহিত্য সম্পর্কে যা বলেছেন
তা হল গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদির উদ্দেশ্য হল মানুষের মনে উদয় হওয়া বা সৃষ্টি হওয়া
ভাব গুলো মন থেকে মনে প্রবাহিত করে দেয়া ও তাকে সময়ের মধ্যে স্থায়িত্ব দেয়া। সাহিত্য
সমাজে মানুষের জীবনাচরণের বিষয়াবলী হতে বেছে নিয়ে তাকে আরো পরিশীলিত করে নতুন ভাবে
প্রকাশ করে। অনেকটা ধুয়ে মুছে নতুন ভাবে প্রকাশ করে। সাহিত্যের সামগ্রী প্রবন্ধটি একটি
মূল্যবান রচনা আর আমার সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানের গোঁড়া বলা যায়। সাহিত্যের সামগ্রী
প্রবন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা ছাড়াও আর কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে বলে আমার
মনে হয়েছে আর তা হল চিন্তনের সাধারণীকরণ বা সার্বিকীকরণ (স্ট্যানডারডাইজেসন আফ থট্স),
চিন্তা-চেতনার সার্বিকীকরণ। আমি যা ভাবছি তা সঠিক কিনা, কোথাও ভুল হচ্ছে কিনা? আর
যদি ভুল থেকেই থাকে তা হলে সেটা কি? এই বিষয়ে সাধারণ স্বীকৃত মতটির যথার্থতা বিচার
করা। এই সব প্রশ্নর সমাধানও লেখালেখির আরেকটি উদ্দেশ্য। সাহিত্য ও সংষ্কৃতি একটি জনগোষ্টির
স্বাস্থ্য সম্পর্কে থারমমিটারের মত কাজ করে। অতি জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেতা আমিতাভ বচ্চনের একটি কথা আমাকে
চমকে দিয়েছিল, সে বলছিল, অভিনেতারা মূলত একটি মাধ্যম বা মিডিয়া, তার কথায় চট করে একটা
জট খুলে গেল, আগে ভাবতাম এত বিভিন্ন চরিত্র এক ব্যক্তি দারুন ভাবে অভিনয় করছে কি ভাবে
আর তাকে অন্য চরিত্রে দেখা সত্যেও এই চরিত্রে আমিই বা কেন তা মেনে নিচ্ছি? অমিতাভ বচ্চনের
কথায় বুঝলাম, অভিনেতা মূলত যে চরিত্রটি চিত্রণ করছে তা সাহিত্যের একটি ধারা বা বলা
যায় অত্যন্ত শক্তিশালী ধারা যার মাধ্যমে একটি তথ্য বা ধারনা বিপুল পরিমাণে জনমনে সঞ্চার
করা সম্ভব হয়। তাই চলচ্চিত্র বা মুভি হল সাহিত্যের সব থেকে বড় বাহন যাকে সর্ববৃহৎ কমপোজিট
আর্টও বলা হয়। এই যে বৃহৎ বুলডোজার আর্ট এর কথা বললাম এটারও শুরু ঐ লেখালেখির মধ্য
দিয়েই। তাই লেখালেখি সম্পর্কে হ্যারি পটারের লেখিকা বা রচয়িতা জে কে রাওলিং এর উক্তি,
“লেখালেখি ভালোবাসার চেয়েও বেশি কিছু। এটা আবশ্যিকতা।”
লেখালেখির প্রচলিত উদ্দেশ্যের পাশাপাশি আরেকটি উদ্দেশ্য আছে
তা হল অন্য একটি বা একাধিক মনের সাথে কানেক্ট করা বা সংযোগ স্থাপন। অন্যর কাছে নিজের
সুচিন্তাটা পৌছে দেয়া ও তার কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করা বা ওই বিষয়ে তার মতামত জানার
প্রত্যাশা। লেখালেখিকে একমুখী ভাবা হলেও আসলে তা দ্বিমুখী (ইন্টার্যাক্টিভ) প্রক্রিয়া।
ফেইসবুকের কোন post এ জানা অজানা কেউ লাইক দিলে মনে কেন আনন্দ উদ্দীপন হয় তা নিয়ে
গবেষনা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে এতে আমাদের দেহ মনে রাসায়নিক পরিবর্তন হয় যা মানুষকে
ক্ষণিক আনন্দ পুলক দেয়, তাই সে তা আরো পেতে চায় আর তার পর তাতে আবিষ্ট হয়ে যায়, মনস্তাত্ত্বিক
গবেষকরা সেই কথাই বলেছেন। আমার কিন্তু আরেকটি কারণ মনে হয়েছে এর পিছনে কাজ করে আর তা
হল, কোন আত্মা তার আকৃতি খুঁজে পায় না যতক্ষণ না সে তার প্রেরিত বার্তার প্রত্যুত্তর
খুঁজে পায়, সে আরেকজনের কাছ থেকে তার কথার, ছবির, কাজের স্বীকৃতি চায় বা তার আলোকে
নিজেকে বিচার করতে চায়। বিষয়টা অনেকটা রাডার স্ক্যানারের মত কাজ করে, ছুঁড়ে দেয়া আলোর
প্রতিবিম্বে নিজের আকৃতি দেখতে পায়। যেহেতু নিজেকে মাপার বা দেখার আর কোন উপায় তার
কাছে নাই। সে ঘুরে নিজেকে দেখতে পায় না তাই অন্যর চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে চায়। আয়নায়
দেখা প্রতিচ্ছবির কথা ভাবছেন? আয়না সব সময় আপনার বিপরীত প্রতিচ্ছবি বা অপজিট প্যারেটি
দেখাবে, ডান চোখ বন্ধ করে দেখবেন আয়নাতে আপনার প্রতিচ্ছবি বাম চোখ বন্ধ করে রেখেছে।
অন্যের চোখই তাই নিজেকে দেখার সঠিক আয়না। লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে পাঠক মহলে মন্তব্য,
সমালোচনা তাই লেখকের আত্ম উপলব্ধিতে অনেক কাজে আসে, ক্রিটিক ভাল হোক বা মন্দ হোক
তার লেখার মান উন্নত করে দেয়। এ বিষয়ে রাওলিং বলেছেন লেখকের সবচেয়ে বড় সমালোচক তার
মনের মধ্যেই বাস করে। বাইরের সমালোচেকের চেয়ে ভিতরকার সমালোচকের প্রতি লেখকের ভয়
বেশী, তাই লেখিকা তাকে বিস্কুট খেতে দেন। ক্লাস এইটে পড়ার সময় একটা চকচকে ছোট নতুন কাচি দিয়ে সাদা কাগজের ঝালর কাটার অভ্যাস তৈরী
হয়েছিল, শুধু ঝালর কাটাই নয় তার একটার চেয়ে আরেকটার সৌন্দর্য বিচার করতে যেয়ে তাকে
শ্রেণীকরণ ও সবচেয়ে সুন্দরটি মাপতে গিয়ে যা বুঝেছিলাম তা হল পরিমাপাক নীতিমালা বা কোন
মানদণ্ড ছাড়া কেবল মনের বিচারে সঠিক মান নিয়ন্ত্রণ বা নির্বাচন সম্ভব নয়। মানবিক বিচার
আর যুক্তির বিচারে বিস্তর পার্থক্য আর তাই সেইটাই সব থেকে ভাল যা মন তার নিজস্ব ভাব
ধারায় সুন্দর বলে বিচার করে। এই বিচার বোধের সাধারণ মানদণ্ডের জনমত (কনসেনসাস) গঠন
করতেও সাহিত্য বিশাল ভূমিকা পালন করে।
লেখালেখির আরেকটি উদ্দেশ্য, মনের ভাবকে ভাষায় রূপান্তর করা।
ভাব প্রকাশের উপায়টাকে রবীন্দ্রনাথ দীঘির সাথে তুলনা করেছেন আর দিঘীর জলকে চিরায়ত জ্ঞানের
বা ভাবধারার সাথে। ভাব প্রকাশের উপায় তা ভাষা হোক, চিত্র কর্ম হোক কিংবা চলচ্চিত্র,
এই উপায়টাই মানুষের সৃষ্টি। সূর্যোদয়ের অনুভব একেক মনে একেক ভাবে প্রতিভাত হতে পারে
তার প্রকাশে ভিন্নতা থকাটাই স্বাভাবিক আর এই শাশ্বত সৌন্দযের অভিব্যাক্তিই সাহিত্য।
রবীন্দ্রনাথ ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতায় মনে উদয় হওয়া ভাবকে প্রকৃত
সত্য বলে উল্লেখ করেছেন, আসলে প্রকৃত মানুষ তো তার মনের ভাবেই বিরাজ করে, ভাষা দিয়ে
সে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় অন্যের কাছে। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্যেও ভাষার শক্তি তাই অনেক।
মনের ভাবকে ভাষায় রূপান্তর লেখালেখির অন্যতম উদ্দেশ্য বলে আমার মনে হয়েছে। নিজে বুঝা
ও অন্যকে বুঝান বা তার মনের ভাবের সাথে মিলায়ে দেখা। মনের বার্তা অন্য মনের কাছে পৌছে
দেওয়া। মনের ভাব তো যুক্তির নীতিতে চলে না আবার যুক্তি ছাড়া তাকে অপরের কাছে বা সবার
কাছে গ্রহনযোগ্যও করা যায় না। এই প্যারাডক্স সমাধানের একমাত্র উপায় এই ভাব বিনিময়ের
মিথষ্ক্রিয়া। যাকে সমাজবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন বাদ-প্রতিবাদ-সংবাদ বা সংলাপ (ডায়ালেকটিক্স)।
নতুন কিছুর উদ্ভাবনই হয় এই ডায়ালেকটিক্সের মাধ্যমে। পুরাতনের সাথে নতুন সম্ভাবনার মিশ্রণেই
ধারাবাহিক উন্নতি সম্ভব। “কলি ফুটেছি কি ফুটে নাই, অলি বার বার ফিরে যায়” আর “আকাশ খুলে বসে আছি, তাও কেন দেখছনা” গান দুটির ভাবার্থ প্রায় একই কিন্তু একটি অতি পুরাতন আরেকটি নতুন। একমাত্র
মানুষ নামক প্রাণীরই একঘেয়েমি জনিত বিরোক্তি বোধের সামর্থ্য আছে, তাই সে সব সময় নতুন
কিছু সৃষ্টির উন্মাদনায় ভুগে। নতুন উদ্ভাবন তাই মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। লেখালেখির
মাধ্যমেই নতুন উদ্ভাবন সম্ভব হয়। এক জায়গায় পড়েছিলাম “কেউ মনে করে না যে, অশ্ব মানব,
পরি, কল্প রাষ্ট্র (ইউটোপিয়া) বাস্তব, তবে মনে করা হয় যে, বাস্তব জগত হতে স্বতন্ত্র
কোন জগতে তাদের অস্তিত্ব আছে আর এভাবেই আলোচনার জগত ধারনাটির উদ্ভব হয়।” একঘেয়েমি জনিত বিরোক্তি বোধের সামর্থ্যর মত কল্পনা করার শিক্তও একমাত্র মানুষেরই
আছে। কল্পনায় ভর করে পুরাতন যুগের অশ্ব মানব হতে আজকের যুগের স্পাইডার ম্যান, সুপারম্যান
এ্যাভেনজারস আর ড্রাকুলারাও বিশ্ব সাহিত্যের জীবন্ত চরিত্র। হলপ করে বলতে পারবেন টম
এন্ড জেরির কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই? বরং তারা এতটাই জীবন্ত যে তার কখনও বিনাস হবে
না। অস্তিত্বের দার্শনিক সত্যাসত্য অত্যন্ত বিতর্কিত একটি বিষয়। বাহ্য আর অন্তস্থ কিংবা
যদি বলি ব্রাক্ষণ ও আত্মন ইংরেজিতে যাকে বলে ‘এ্যাপিয়ারেন্স’ আর ‘দ্যা থিং ইন ইটসেল্ফ’ এর প্যারাডক্সটা এই বিশ্বজগতে
কখনই সমাধান যোগ্য হবে বলে মনে হয় না। এই দ্বন্দ্ব না থাকলে সকলের মন একই রকম হয়ে
যেত অনেকটা জীবন শূন্য ধুসর মরুর মত। তাই খানিকটা অসংগতি ও তন্ময়তার ভাব মানব সঞ্জায়
সংযুক্ত করা আছে। থাকাটাই ভাল, মানব মনের তন্ময়তাকে কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে যান্ত্রিক
মানব সৃষ্টি করা যাবে ঠিকই কিন্তু তাতে মানবতা ধ্বংস হয়ে যাবে।
মনের গভীরতায় বা চিন্তার জগতে ডাইভ বা ড্রাইভ দেয়া একটি চমকপ্রদ
ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাও বটে। যার মন যত তথ্য বহুল তার তত বিস্তৃত বিচরণ ক্ষমতা। সৈয়দ
মুজতবা আলীর গল্পের সেই বই পড়া আর মাছির পুঞ্জাক্ষীর সাথে তুলনা করা এর সাথে মিলে যায়।
লেখালেখির পাশাপাশি বই পড়ার অভ্যাসটাও তাই জরুরী। বই পড়া ছাড়া যদি আপনি চিন্তার জগতে
ডাইভ দেন তবে নির্ঘাত পথ হারাবেন। মনের ভুবন হাজার কোটি মহাবিশ্বর চেয়েও বড় বলে মানব
মন ভাবতে পছন্দ করে। এক সময়কার সাহিত্য আরেক সময়ের সাহিত্যের সাথে মিলবে না আবার এক
এলাকার সাহিত্য অন্য এলাকার সাহিত্যর সাথেও মিলবে না কিন্তু বিশ্বসাহিত্যর সাধারনিকৃত
রূপ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন এলাকার মানুষের চিন্তুা ভাবনা একই রকম হওয়ার ও
তো কথা নয়। তবে মনে রেখাপাত করে সেই সাহিত্য যা সাম্প্রতিক বাস্তবতা ও মানুষের জীবনাচরণের
সাথে মিলে যায়। রবীন্দ্র রচনা আর নজরুল রচনার পার্থক্যটা খেয়াল করলেই বুঝা যায় প্রত্যেক
মানুষের মনোভঙ্গির একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, হুবহু একই রকম কখনই হবে না তার পরও বিশ্বায়নের
এই যুগে সকল মানুষের জীবনাচরণের ও চিন্তা ভাবনার মধ্যে একটি একক ধারায় বিবর্তন শুরু
হয়ে গেছে। মহাকালের ধারায় বিশ্ব সাহিত্যের এই একীভূতকরণ প্রক্রিয়াই এখন সাহিত্যের প্রকৃত
বাস্তবতা। গানে যা বলা হচ্ছে কিংবা গল্প, নাটক, চলচ্চিত্র এ সবের আরেক দিক শিক্ষাদান
এই আর্থে যে তা স্টেনডারডাইজ করে ও নতুন রূপকল্প প্রস্তাব করে। আমরা অনেকে মন খুলে
কথা বলি না হয়ত এই কারনে যে, কে কি মনে করে, পাছে লোকে আময় মূর্খ ভাবে, অবমূল্যায়ন
করে কিংবা আমার মনের কথা বুঝে আমার ক্ষতিসাধন করে, এইসব হাবিজাবি অযথা কারণে, অনেকের
অবশ্য অভ্যাস আছে মনটাকে চিন্তামুক্ত রাখার, তারা মন চিন্তুাশুন্য করে মনকে প্রশান্ত
রাখার চেষ্টা করে। আমার এক বন্ধু বলতো চিন্তা করলেই তার মাথা ধরে, ও মূলত সকল চিন্তাকেই
দুশ্চিন্তা মনে করত। এ রকম যারা তারা কি জীবনের মৌলিক চিন্তু গুলো যা মানব সভ্যতা
আজও সমাধান করতে পারেনি তা থেকে মুক্তি পায়? জনাব হকিংস তার শেষ গ্রন্থ ‘থিওরি অফ এভরিথিং’ এ বার বার স্রষ্টার প্রসঙ্গে টেনে এনেছে বলে সমালোচিত হল, আর অতি ব্যক্তিত্ব,
বা উচ্চতর মানব হওয়ার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, মাদার তেরেসারা করেছেন কিন্তু
মানব সভ্যতার এই ২০০০ বছরের লিখত ইতিহাস ছাড়াও আরও প্রায় ৬০০০ বছরের পুরাতন প্রত্নতত্ত্ব
যুগের মানুষ আর এখনকার মানুষে পার্থক্যটা ভেবে দেখুন? চিন্তা-চেতনায় এখনকার মানুষেরা
কতটাই না এগিয়ে গেছে। মত প্রকাশে অনীহা মানে হল আপনি নিজেকে ও অন্যকে অবহেলা করছেন
আর সভ্যতার বিকাশে আপনার অংশগ্রহণকে অস্বীকার করছেন। মানব যোগাযোগের ক্ষেত্রে মৌন
থাকাটা তাই একটা অপরাধ।
লিখালিখির আরেকটি উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশের বাসনা যা একটি শক্তিশালী
মানব প্রবৃত্তি বা ইনিসটিং। বারট্রান্ড রাসেলের বই ‘অরাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি-প্রবৃত্তি’বইটি ছাড়াও ম্যকিয়াভেলি বা ম্যাসল’স হাইয়ারারকী অব নিড্স, কিংবা ইমাম গাজ্জালীর মানব প্রবৃত্তির উপর বক্তব্য গুলো
ম্যাস আপ করলেও এই বক্তব্যই পাওয়া যাবে। আত্মপ্রকাশ বা নিজেকে অন্যর কাছে প্রকাশ করার
চিরন্তন মানব প্রবণতাও লিখালিখির আরেকটি উদ্দেশ্য। আত্মপ্রকাশ, মানব সংযোগ, সমাজ গঠন,
আত্মউন্নয়ন এরকম প্রায় সব মানবিক ক্ষেত্রেই লেখালেখির বিশেষ অবদান আছে। আত্মপ্রকাশ
না করলে একের মতের সাথে অন্যর মত মিলবে কিভাবে ? সমাজ বা সংঘ সংগঠনের প্রথম ধাপই তাই
এই লেখালেখি। আমার খালার ঘনিষ্ট বান্ধবীর মামা তখনকার জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আহসান আলী’র ‘পূর্ব বাংলা’ কবিতার সেই লাইনটা এখনও মনে রেখাপাত
করে, “আমার পূর্ব বাংলা, অনেক পাতার ঘনিষ্টতায় এক প্রগাড় নিকুঞ্জ”। ভাগ্য ভাল উনি লিখেন নাই আমার সোনার বাংলা অনেক নৌকার ঘনঘটায় এক প্রকাণ্ড
কর্মযজ্ঞ। সাহিত্যের রাজনীতিকরন করা উচিত না আর তা করলে প্রকৃত সাহিত্য হবে না। উদ্দেশ্য
প্রণদিত ভাবে লেখালেখিকে ব্যবহার করে যারা রাজনৈতিক মত প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিংবা কিছু
অসাধু সাংবাদিক যারা অন্যের দুর্বলতা প্রকাশ করে তাকে বিপদের ভয় দেখিয়ে টাকা কামাই
করেত চায় তারা সাহিত্যের কাল বাজারী। আর যারা লেখালেখিকে বানিজ্যিকী করণ করেছেন, যুব
মানসকে পুঁজি করে প্রকাশক ও নিজের জন্য বিপুল সম্পদ আয়ত্ত করার উপায় খুঁজে পেয়েছেন
তাদের সম্পর্কে আমার কিছুই বলার নাই। সমাজের সুস্থ মানুষ গুলোই তার বিচার করবে আর
কালের বিচারে তাদের কাজের গুরুত্বও কমে যাবে। তন্ময়তার ভাষাই প্রকৃত সাহিত্য, তা-ই
আমাদের সংস্কার বা সংস্কৃতি হওয়া উচিত।
আমার লেখা-লেখির উদ্দেশ্যটা এবার বলে ফেলি? মনে অনেক কথা
আর চিন্তার জটাজাল, এই চিন্তার জটিলতা সরলীকরণের জন্যই লিখে চিন্তা করার চেষ্টা, বিশ্লেষনে
সময় লাগে, লিখলে তা সহজ হয়। আত্মসমালচনা, আত্মকথন আর যথার্থতার মানদণ্ড বা বিবেক গঠনের
প্রয়োজনেই লিখতে থাকি। তাছাড়া মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে নিষঙ্গ, সে বড় একা, তার বসবাস মনোজগতে
আবদ্ধ, বহির্বিশ্বে তার বিস্তারের একটাই উপায় আছে আর তা হল অন্যের মনের সাথে ভাব বিনিময়
করা। শেষ করতে চাই এই বলে, মন খুলে কথা বলুন, নিজের মতকে সবার কাছে প্রকাশ করে দিন
তা ভাল হোক আর মন্দ হোক কিচ্ছু যায় আসে না, আপনার আমার সবার জন্য তা অবশেষে ভালই
হবে। এতে করে সম্মিলিত ও সামগ্রিক মানব আত্মা তথা মানব সভ্যতা সমৃদ্ধ হবে। কিছু দিনের
মধ্যেই আমি আপনি মহাকালের চোরাবালীতে বিলীন হয়ে যাব কিন্তু আমাদের কথাগুলো বা ভাবনা
গুলো হয়ত মন থেকে মনে বিরাজ করতে থাকবে, আর এটাই চিরন্তন বিশ্ব মানবতা।
এডিট ও আপডেট হিস্ট্রিঃ ০৩সেপ্টেম্বর২০১৯> ১৯সেপ্টেম্বর২০১৯> ১১ডিসেম্বর২০২৩>